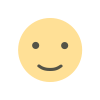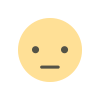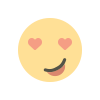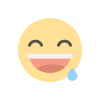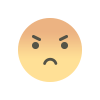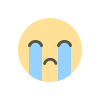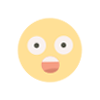জন্মশত বর্ষ । ইলা মিত্র আমাদের নিত্য প্রেরণার উৎস । সোহরাব হাসান

ইলা সেন নামে যে মেয়েটি ১৯২৫ সালের ১৮ অক্টোবর জন্ম নিয়েছিলেন, তিনি হয়ে উঠলেন আমাদের ইতিহাসের কিংবদন্তী—ইলা মিত্র। তাঁর পৈত্রিক বাড়ি ঝিনাইদহের বাগুটিয়া গ্রামে; কিন্তু তাঁর জন্ম, বেড়ে ওঠা ও পড়াশোনা কলকাতায়। বাবা নগেন্দ্রনাথ সেন ছিলেন বাংলার উপপ্রধান হিসাবরক্ষক।
ইলা মিত্র ছিলেন নামকরা ক্রীড়াবিদ। ১৯৪৫ সালের বিশ্ব অলিম্পিকে জাপান যাওয়ার কথা ছিল, যদিও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে সেই আয়োজন সম্ভব হয়নি। ইলা মিত্র পাঠ নিয়েছেন কলকাতার বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেথুন স্কুল ও কলেজে, পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে।
শৈশব বা কৈশোরে বর্তমান বাংলাদেশের সঙ্গে ইলা মিত্রের সরাসরি যোগাযোগ ছিল না। কিন্তু সেই যোগাযোগ গড়ে ওঠে ২০ বছর বয়সে, যখন জমিদার তনয় রমেন মিত্রের সঙ্গে বিয়ে হয়। রমেন মিত্রের বাবা ছিলেন চাপাইনবাবগঞ্জ জেলার রামচন্দ্রপুরের জমিদার। বিয়ের পর ইলা মিত্র কলকাতা ছেড়ে শ্বশুরবাড়িতে আসেন। কলকাতায় তাঁর ছিল মুক্ত জীবন। এখানে অনেকটা বন্দী জীবন। জমিদার বাড়ির পুত্রবধূ গ্রামের আর পাঁচজনকে মুখ দেখাবেন, সেটা কোনোভাবেই মানতে পারছিলেন না অভিভাবকেরা।
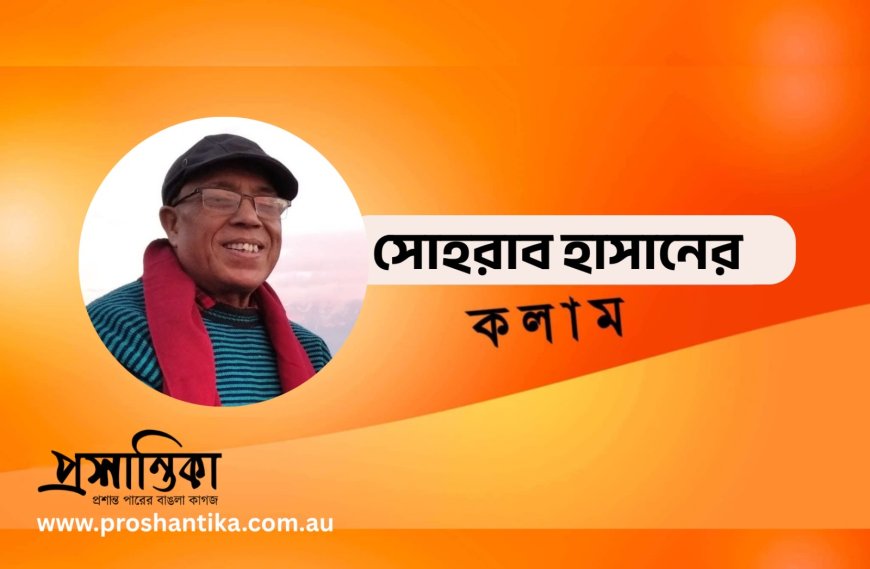
কিন্তু ইলা তো লড়াকু মেয়ে। তিনি ঘরে বসে থাকতে পারেন না। স্বামী রমেন মিত্রের বন্ধু আলতাফ হোসেন প্রস্তাব দিলেন তিনি গ্রামে একটি বালিকা বিদ্যালয় গড়ে তুলবেন, ইলা মিত্র হবেন তার প্রধান শিক্ষয়ত্রী। প্রথমে শিক্ষার্থী ছিলেন তিনজন। ছয় মাসের মধ্যে সংখ্যা দাঁড়াল ৪০–এ। জমিদার বাড়ির সম্মান রক্ষার জন্য প্রথম দিকে ইলা মিত্রকে গরুর গাড়িতে চড়েই বিদ্যালয়ে যেতে হতো। মাস তিনেক পরে পায়ে হেঁটে যাওয়ার অনুমতি পান। ইতিমধ্যে হেডমিস্ট্রেস হিসেবে তাঁর নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।
নাচোল উপজেলার কেন্দুয়ায় কেন্দুয়া পঞ্চানন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে ইলা মিত্রের স্মৃতিস্তম্ভটি এখনো নাচোলের কৃষক বিদ্রোহের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সেখান থেকে যাওয়ার সময় পথচারীরা ক্ষণিকের জন্য হলেও থমকে দাঁড়ান এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা অবনত করেন। আজ সেই মহান নেত্রীর জন্মশত বর্ষ।
চাঁপাইনবাবগঞ্জের ইতিহাসে জড়িয়ে আছে তাঁর নাম। ১৯৪৬–১৯৫০ সালে নাচোলের তেভাগা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ১৯৪৩ সালে তিনি কলিকাতা মহিলা সমিতির সদস্যপদ লাভ করেন। ‘রাওয়াল বিল’ বা হিন্দু কোড বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলনেও ছিল তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।
১৯৪২ সালে এ দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। তখন কৃষকদের উপর শোষণের মাত্রা বেড়ে যায়। কৃষকরা শুরু করে ‘তিন ভাগের দুই ভাগ ফসল’-এর জন্য আন্দোলন। এই আন্দোলন চলে ভারত–পাকিস্তান বিভক্তির পরেও। কৃষকদের প্রতিরোধের মুখে আপাতভাবে তেভাগা কার্যকর করা হলে ভূমিমালিকরা থেমে থাকেনি। সরকারের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী নানা ভাবে কৃষকদের ওপর অত্যাচার-নিপীড়ন চালাতে থাকে। এক পর্যায়ে এক পুলিশ কর্মকর্তা ও ৫ জন কনস্টেবল নিহত হয় আন্দোলনকারীদের হাতে।
রমেন্দ্র মিত্রও ছিলেন স্বাধীনচেতা মানুষ। ফ্লাউড কমিশন রিপোর্ট বাস্তবায়ন এবং কৃষকদের জমি ভাগাভাগির বিষয় দু’টি নিয়ে পুরো দেশ তখন সরকারবিরোধী আন্দোলনে উত্তাল। নাচোলের কৃষকরাই ছিল আন্দোলনের পুরোভাগে। এই আন্দোলনের সামনের সারিতে ছিল সাঁওতালরা।
১৯৫০ সালের ৫ জানুয়ারি পুলিশ ও কৃষকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এরই জের ধরে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার দুই দিন পর নাচোলে প্রায় ২ হাজার সেনা প্রেরণ করে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য। কিন্তু সেনারাও এলাকায় ব্যাপক মারপিট করে এবং গুলি করে শতাধিক ব্যক্তিকে হত্যা করে এবং জ্বালিয়ে দেয় ১২টি গ্রামের কয়েক শত বাড়ি-ঘর। এদের বেশিরভাগই ছিল সাঁওতাল অধিবাসী। পাকিস্তানি সৈন্য এবং পুলিশের অত্যাচারে প্রতিটি পরিবারের সকল সদস্য এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। ইলা মিত্রও সাঁওতালদের পোশাক পরে পালিয়ে যান। পোশাক বদলালেও ভাষাগত কারণে গোয়েন্দা পুলিশের হাতে ইলা মিত্র বিপুল সংখ্যক অনুসারীসহ গ্রেফতার হন রহনপুর থেকে।
নাচোল থানায় তাঁর উপর চলে পুলিশি অমানুষিক নির্যাতন। প্রথম ধাপে টানা চার দিন চলে এই নির্যাতন। প্রচণ্ড জ্বর ও রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে নেওয়া হয় চাঁপাইনবাবগঞ্জ হাসপাতালে। ওই মাসেই ২১ তারিখে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ এনে তাঁকে রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আর সেখানেই শুরু হয় নির্যাতনের দ্বিতীয় ধাপ।
এই নির্যাতন সম্পর্কে ইলা মিত্র রাজশাহী আদালতে যে ঐতিহাসিক জবানবন্দী দিয়েছিলেন তা ইতিহাসের অংশ হয়ে গেছে। তিনি লিখেছেন:
“কেসটির ব্যাপারে আমি কিছু জানি না। বিগত ০৭/০১/১৯৫০ তারিখে আমি রহনপুরে গ্রেফতার হই এবং পরদিন আমাকে নাচোল নিয়ে যাওয়া হয়। যাওয়ার পথে পুলিশ আমাকে মারধর করে এবং তারপর আমাকে একটা সেলের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশ হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে সবকিছু স্বীকার না করলে আমাকে উলঙ্গ করে দেওয়া হবে বলে এসআই হুমকি দেখায়। আমার যেহেতু বলার মতো কিছু ছিল না, কাজেই তারা আমার সমস্ত কাপড়-চোপড় খুলে নেয় এবং সম্পূর্ণ উলঙ্গভাবে সেলের মধ্যে আমাকে বন্দী করে রাখে। আমাকে কোনো খাবার দেওয়া হয়নি, এক বিন্দু জলও নয়। সেদিন সন্ধ্যা বেলাতে এসআইয়ের উপস্থিতিতে সেপাইরা তাদের বন্দুকের বাঁট দিয়ে আমার মাথায় আঘাত শুরু করে… তারা অমানুষিক নির্যাতন চালায়। সেলে চারটে গরম সেদ্ধ ডিম আনার হুকুম দিল। তারপর চার-পাঁচজন সেপাই আমাকে জোরপূর্বক ধরে চিৎ করে শুইয়ে দেয় এবং একজন আমার যৌনাঙ্গের ভিতর একটা ডিম ঢুকিয়ে দিল। আমি আগুনে পুড়ে যাচ্ছিলাম। এর পর অজ্ঞান হয়ে পড়ি। ৯ জানুয়ারি ১৯৫০ সকালে যখন আমার জ্ঞান হলো তখন উপরোক্ত এসআই এবং কয়েকজন সেপাই আমার সেলে এসে তাদের বুট দিয়ে আমাকে চেপে লাথি মারতে শুরু করল। এরপর আমার ডান পায়ের গোড়ালিতে একটা পেরেক ফুটিয়ে দেওয়া হলো। সেই সময় আধাচেতন অবস্থায় পড়ে থেকে আমি এসআইকে বিড়বিড় করে বলতে শুনলাম, ‘আমরা আবার রাত্রিতে আসছি এবং তুমি যদি স্বীকার না কর তাহলে সেপাইরা একে একে তোমাকে ধর্ষণ করবে।’ গভীর রাত্রিতে এসআই এবং সেপাইরা ফিরে এলো এবং তারা আবার সেই হুমকি দিল। কিন্তু যেহেতু তখনও কিছু বলতে রাজি হলাম না তখন তিন-চারজন আমাকে ধরে রাখল এবং একজন সেপাই সত্যি সত্যি ধর্ষণ করতে শুরু করল। এর অল্পক্ষণ পরই আমি অজ্ঞান হয়ে পড়লাম। পরদিন ১০ জানুয়ারি যখন আমার জ্ঞান ফিরে এলো তখন আমি দেখলাম যে আমার দেহ থেকে দারুণভাবে রক্ত ঝরছে এবং কাপড়-চোপড় রক্তে সম্পূর্ণ ভিজে গেছে। এর পর আমাকে নবাবগঞ্জ হাসপাতালে পাঠানো হলো এবং ২১ জানুয়ারি নবাবগঞ্জ থেকে রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে নিয়ে এসে সেখানকার জেল হাসপাতালে ভর্তি করা হলো… কোনো অবস্থাতেই আমি পুলিশকে কিছু বলিনি।”
এর পর ইলা মিত্রকে পাঠানো হয় ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে। সেখানে নির্যাতনের তৃতীয় ধাপ চলে। মুমূর্ষু অবস্থায় ইলা মিত্রকে চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। অবস্থা গুরুতর দেখে ১৯৫৪ সালের ৫ এপ্রিল তৎকালীন যুক্তফ্রন্ট সরকারের পাঁচ সদস্যের এক কমিটি ইলা মিত্রের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে একটি প্রতিবেদন দাখিল করে। এতে বলা হয়—কোনো ধরনের শর্ত ছাড়া যদি ইলাকে মুক্তি দেওয়া না হয়, তাহলে তাঁকে প্রাণে বাঁচানো যাবে না।
ইলা মিত্রকে দেখতে তখন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে শত শত ছাত্র-ছাত্রী, রাজনীতিবিদ, শিক্ষক, সাংবাদিকসহ সুশীল সমাজের লোকজন ছুটে যায়। শেষ পর্যায়ে সরকার তাঁকে প্যারোলে মুক্তি দিয়ে কলকাতা যাওয়ার অনুমতি দেয়। এর পর তিনি আর ফিরে আসেননি বা আসতে পারেননি। পাকিস্তান সরকার তাঁর ও রমেন মিত্রের বিরুদ্ধে যে হত্যা মামলা করেছিল, তা কখনো প্রত্যাহার করা হয়নি। স্বাধীনতার পর ইলা মিত্র বাংলাদেশে এসে মামলার বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। উত্তরে তিনি বলেছিলেন—“এখন সেই মামলা আছে কি? সেটা তো ইলা মিত্রের পক্ষে বলা সম্ভব নয়। বলতে পারে বাংলাদেশ সরকার।”
ভারতেও ইলা মিত্রকে নানা রকম রাজনৈতিক হয়রানির মধ্যে পড়তে হয়। পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস সরকার তাকে চারবার গ্রেপ্তার করে। সরকারের অত্যাচার-নির্যাতন সত্ত্বেও ইলা মিত্র তাঁর নীতি ও আদর্শের রাজনীতি থেকে সরে যাননি। ১৯৬২ থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত তিনি মানিকতলা আসন থেকে চারবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তিনি সক্রিয় সহযোগিতা করেন।
কর্মজীবনে ইলা মিত্র কলকাতা সিটি কলেজের বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপিকা হিসেবে ১৯৮৯ সালে অবসর নেন। রাজনীতির পাশাপাশি সাহিত্য চর্চায়ও ছিল তাঁর বিশদ ব্যপ্তি। ‘হিরোশিমার মেয়ে’ গ্রন্থ অনুবাদের জন্য তিনি ‘সোভিয়েত লেনিন-নেহরু’ পুরস্কার পান। ব্রিটিশ শাসনবিরোধী দীর্ঘ সংগ্রামী আন্দোলনে সফল নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় ভারত সরকার তাঁকে ‘তাম্রপত্র অ্যাওয়ার্ড’ প্রদান করে। ৭৭ বছর বয়সে ২০০২ সালের ১৩ অক্টোবর তিনি মৃত্যুবরণ করেন।
এ বছর ইলা মিত্রের জন্মশত বর্ষ। পশ্চিমবঙ্গ বা ভারতবর্ষ তাঁর জন্মশত বর্ষ কীভাবে উদযাপন করল, সেটা তাদের বিষয়। কিন্তু যেই মানুষটি আমাদের ইতিহাসের অংশ, যিনি তেভাগা আন্দোলন করতে গিয়ে তৎকালীন মুসলিম লীগ সরকারের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁকে রাষ্ট্রীয় ও জনপরিসরে স্মরণ করা আমাদের কর্তব্য।
ইলা মিত্র তেভাগা আন্দোলন শুরু করেন ১৯৪৬ সালে। মুসলিম লীগ সরকারের পতন ঘটে ১৯৫৪ সালে। মুসলিম সরকারের পতনের কারণেই তিনি কারাগার থেকে মুক্ত হন এবং চিকিৎসার জন্য কলকাতায় চলে যান।
ইলা মিত্রের সংগ্রামী জীবন কেবল নাচোল থেকে শুরু হয়নি। শিক্ষার্থী থাকা অবস্থায় যখন ১৯৪৩ সালে দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, আরও অনেকের সঙ্গে বিপন্ন মানুষকে বাঁচাতে এগিয়ে আসেন। এ সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের লেখক শর্মিষ্ঠা দত্তগুপ্ত লিখেছেন, “আমি ভাবছি, ১৯৪৩ সালে বেথুন কলেজে পড়ুয়া একটি ১৮ বছরের মেয়ের কথা। যাতায়াতের পথে চোখ পড়ত কলেজের সাথেই ছিল একটি লঙ্গরখানা। মনে মনে অস্থির হয়ে ওঠা সেই মেয়েটি সেখানে গিয়ে কথা বলে, কিছু করতে চায় দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের জন্য। সেই থেকে যুক্ত হয়ে যায় প্রথমে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির দুর্ভিক্ষ ও যুদ্ধবিরোধী কাজে, পরে কমিউনিস্ট পার্টিতে।”
ইলা মিত্র চুয়ান্ন সালে চিকিৎসার জন্য কলকাতায় গিয়ে দেশে ফিরে আসতে না পারলেও তাঁর প্রিয় পূর্ববঙ্গের কথা কখনো ভুলতে পারেননি। একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধের ছয় বছর আগে, ১৯৬৫ সালে ‘কালান্তর’-এ লিখেছিলেন—“পূর্ববঙ্গ আজও আমার তীর্থভূমি।” দেশত্যাগের স্মৃতি স্মরণ করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন:
তাঁর সফরসঙ্গী পাকিস্তান সরকারের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন—“এই মাটির প্রতি ভালোবাসা ভুলে যাবেন না তো?” তিনি অনুরোধ জানিয়েছিলেন আবার যেন ফিরে আসেন। পাকিস্তানে তাঁর মতো কন্যাদের প্রয়োজন আছে। এই লেখায় ইলা মিত্র পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর নির্যাতনের কথা বলছেন সত্য; কিন্তু তার চেয়েও স্মরণ করেছেন এখানকার সর্বস্তরের মানুষের ভালোবাসার কথা। স্মরণ করেছেন সেই পুলিশ কর্মকর্তাদের, যাদের মধ্যে একজন তাঁর কানের কাছে মুখ এনে বলেছিলেন—ও রকম কাগজে যেন তিনি সই না দেন। তিনি লিখেছেন—“আমাদের মুক্তির জন্য পাকিস্তানে প্রবল আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছিল, যার তুলনা বিরল। ফলে ছাড়া পাওয়ার আগেই মুক্ত মানুষের মধ্যে আমি এমনভাবে মিশে যেতে পেরেছিলাম, যা আরও জমকপ্রদ। ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালে তখন আমি কড়া পাহারায় বন্দী। তবু দলে দলে মানুষ দূর দূর গ্রাম থেকেও হাসপাতালে উপস্থিত হতে থাকল। তখন আমার পাহারারক্ষী জনস্রোতের ধাক্কায় কোথায় তলিয়ে গেল, আমি সমুদ্রে মিশে গেলাম।”
হাসপাতালে তাঁর সঙ্গে স্বামী রমেন মিত্রের সাক্ষাতের বর্ণনা পাওয়া যায় সদ্যপ্রয়াত লেখক ও ভাষা সংগ্রামী আহমদ রফিকের স্মৃতিচারণে। তিনি লিখেছেন:
“ঢাকা মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের ২০ নম্বর ব্যারাকের ৬ নম্বর রুমে বসে আছেন আত্মগোপনে থাকা কমিউনিস্ট নেতা রমেন মিত্র। বেশ কিছু দিন থেকে এ রকম তাঁর যাতায়াত। উদ্দেশ্য একটাই—মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি গুরুতর অসুস্থ স্ত্রী ইলা মিত্রের সঙ্গে রাতে একবার দেখা করা। সময়টা ১৯৫৩ সালের নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি। জনৈক পার্টি নেতার অনুরোধে ইলা মিত্রের দায়টা আমার কাঁধেই থাকে। বড় সুবিধা হলো—পাহারাদার পুলিশটি তাঁর রোগীকে সারাক্ষণ নজরে রাখা আর দরকার মনে করেনি। এখানে সেখানে আড্ডা দিয়ে চা–সিগারেট খেয়ে সে ও বদলি পাহারাদার দিব্বি আরামে সময় কাটিয়েছে। তাই হাসপাতালে রমেন মিত্রকে যেতে মোটেই অসুবিধা হয়নি। রমেন মিত্র হাসপাতালে রোগীর সঙ্গে দেখা করেছেন ‘রমজান মিয়া’ নামে।”
স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় কলকাতায় ইলা–রমেনের বাড়িটি ছিল বাংলাদেশি শরণার্থীদের জন্য বড় আশ্রয়কেন্দ্র। বিশেষ করে কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা সেই বাড়িকেই অস্থায়ী কার্যালয় হিসেবে ব্যবহার করতেন। ইলা মিত্র কিংবা রমেন মিত্র কেউ আপত্তি করেননি। পরবর্তী কালে যখনই বাংলাদেশ থেকে কেউ তাঁদের সঙ্গে দেখা করেছেন, তাঁরা দু’জনই তাঁদের গ্রহণ করেছেন পরম আত্মীয়ের মতো।
ইলা মিত্রের জন্মশত বর্ষ আমরা উদযাপন করব—কেবল এই মহান নেত্রীকে স্মরণ করতে নয়, অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে। ইলা মিত্র আমাদের নিত্য প্রেরণার উৎস।