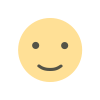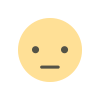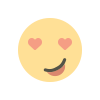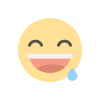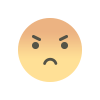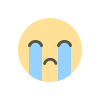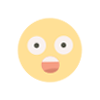সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের শিক্ষা দর্শন ও অলস দিনের হাওয়া । সোহরাব হাসান
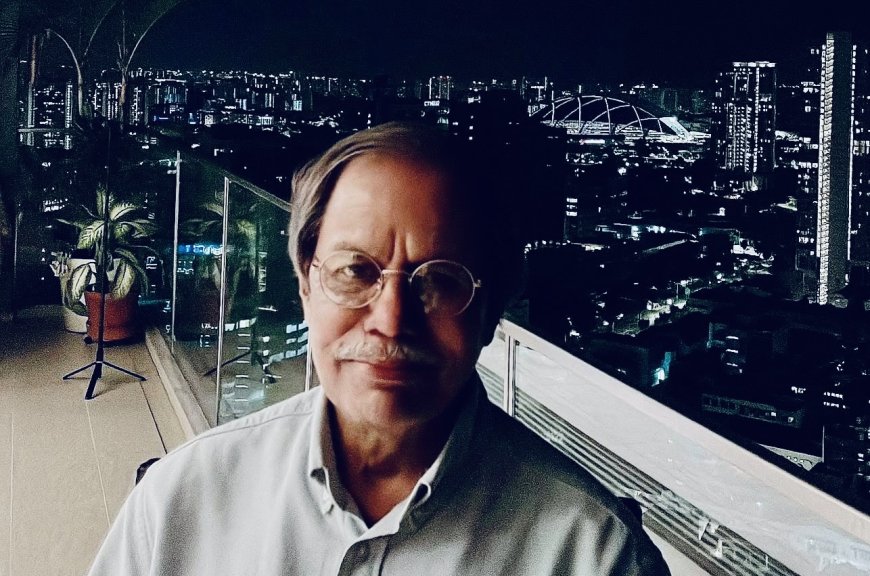
অসংখ্য সাহিত্যপ্রেমী ও শিক্ষার্থী-সুহৃদের আশা গুড়িয়ে দিয়ে চলে গেলেন লেখক-শিক্ষাবিদ সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম। এক মাসেরও কম সময়ের ব্যবধানে তিন কৃতী মানুষকে বিদায় দিতে হলো: প্রথমে বদরুদ্দীন উমর—বামপন্থী চিন্তক ও গবেষক, ৯৪ বছর বয়সে; এরপর গেলেন বায়ান্নর অন্যতম ভাষাসংগ্রামী ও লেখক আহমদ রফিক। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৬ বছর। তুলনায় সৈয়দ মনজুরুল ইসলামকে হারালাম মাত্র ৭৪ বছর বয়সে। একে আমরা অকালপ্রয়াণই বলব।
হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে যখন সৈয়দ মনজুর হাসপাতালে ভর্তি হলেন, তখন আমরা কায়মনো বাক্যে প্রার্থনা করেছিলাম, তিনি আবার আমাদের মাঝে ফিরে আসবেন। এমনকি লাইফ সাপোর্টে নেওয়ার পরও আশা ছাড়িনি; এ রকম জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণ থেকে আমাদের অনেক প্রিয়জন ফিরে এসেছেন। কিন্তু সৈয়দ মনজুর ফিরলেন না।
কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে যেদিন তাঁর মরদেহ রাখা হলো, বৃষ্টি উপেক্ষা করে শত শত ভক্ত-সুহৃদ এসেছিলেন শেষবারের মতো শ্রদ্ধা জানাতে। বৃষ্টি না হলে হয়তো পুরো ঢাকা শহরের বৌদ্ধিক মানুষকে সেখানে পেতাম।
সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জনপ্রিয় শিক্ষক ছিলেন, সভা-সেমিনারে তুখোড় বক্তা। বক্তৃতা দিতেন মননশীল ও সৃজনশীল সাহিত্য রচনায়; সমকালে তাঁর তুলনা মেলা ভার। তিনি একই সঙ্গে বাংলা ভাষায় শিল্পকলার মতো জটিল বিষয়াবলি সহজ ভাষায় পাঠককে বুঝিয়ে দিতে পারতেন। বাংলাদেশের কথাসাহিত্যকে তিনি অন্য মাত্রায় নিয়ে গিয়েছেন। তাঁর ছোটগল্প বা উপন্যাস মার্কেজ, বোর্হেসদের কথা মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু এটাই তাঁর সম্যক পরিচয় নয়।
শিক্ষায়তন কিংবা শিক্ষা-আয়তনের বাইরে আমরা যারাই তাঁর সান্নিধ্যে এসেছি, তাঁর সহৃদয়তার কথা ভোলার নয়। সমবয়সী, বয়োজ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ—সবার প্রিয় মানুষ ছিলেন তিনি। ভালোবাসার মানুষ।
সৈয়দ মনজুরের লেখালেখির সঙ্গে আমাদের পরিচয় ছাত্রাবস্থায়। আশির দশকে বিদেশ থেকে ফিরে আসার পর তিনি বিশ্বসাহিত্য নিয়ে সংবাদ সাময়িকী-তে ধারাবাহিক কলাম- অলস দিনের হাওয়া লিখতে শুরু করলে সেই পরিচয় আরও গাঢ় হয়। তাঁকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয় নব্বই দশকে, যখন শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে জাহানারা ইমামের নামে হল করার বিরুদ্ধে একটি গোষ্ঠী মাঠে নেমেছিল। তাদের তৎপরতা রুখে দিতে ঢাকা থেকে হুমায়ূন আহমেদ একটি দল নিয়ে ট্রেনযোগে সিলেট গিয়েছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের তৎকালীন ট্রাস্টি আক্কু চৌধুরীর অনুরোধে আমরাও সেই ট্রেনযাত্রায় সঙ্গী হয়েছিলাম। সৈয়দ মনজুর আলাদাভাবে গিয়েছিলেন।
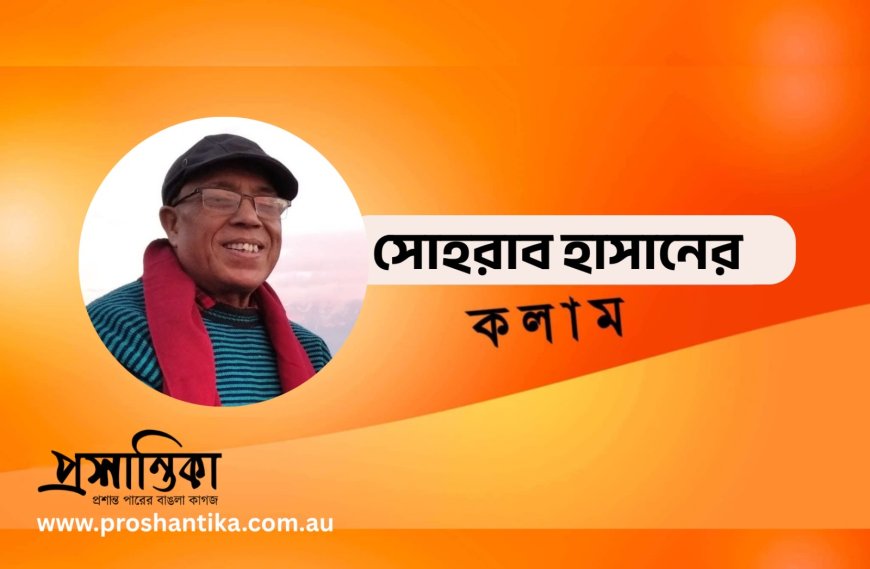
এরপর ২০০৮ সালে কলকাতা বইমেলায় তাঁর সফরসঙ্গী হিসেবে কয়েকটি দিন বেশ আনন্দে কেটেছে। তাঁর সঙ্গে সফর আনন্দদায়ক হওয়ার আরেকটি কারণ—শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতির সব শাখায় তাঁর অবাধ বিচরণ। বৈঠকী আলোচনায়ও তিনি সবার মধ্যমণি।
কলকাতা বইমেলায় বাংলাদেশ প্যাভেলিয়নটি খুব আকর্ষণীয় নয়। আমলা আয়োজিত অনুষ্ঠানও গতানুগতিকতার বাইরে যেতে পারে না। তারপরও সেবার সৈয়দ মনজুরের কারণে সেমিনারটি প্রাণবন্ত হয়েছিল। বইমেলার বাইরে কলকাতার বৌদ্ধিক মহলের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি উত্তর-পূর্ব ভারত তথা গৌহাটিতে কোনো অনুষ্ঠানে একত্রে যাওয়ার কথা বলেছিলেন। সেটা আর হয়নি।
তবে একবার ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস–এ তাঁর আমন্ত্রণে গিয়েছিলাম। অনুরোধে আমার একাধিক কবিতাও অনুবাদ করে দিলেন। কলকাতার সেই যাত্রাটি আরও উপভোগ্য হয়েছিল নাট্যব্যক্তিত্ব রামেন্দু মজুমদারের উষ্ণ সান্নিধ্যে। রামেন্দু দা নাটকের কোনো কাজে কলকাতায় গিয়েছিলেন; তিনি তো আমাদের পেয়ে উচ্ছ্বসিত।
একবার প্রথম আলো-এর পক্ষ থেকে সৈয়দ মনজুরুল ইসলামকে অন্য আলো-র পাশাপাশি উপসম্পাদকীয় কলামে লেখার অনুরোধ জানালে তিনি সানন্দে রাজি হন। তাঁর কলাম প্রথাগত ছিল না। হাস্যকৌতুক ও শ্লেষের সমাহারে তিনি সমাজের সমস্যাগুলো তুলে ধরতেন। কাউকে ব্যক্তিগত আক্রমণ না করেও কঠিন সত্য কথাটি বলতেন।
মনে আছে, বাংলা ভাষার বিকৃত ব্যবহার ও উচ্চারণ নিয়ে তাঁর একটি লেখা নিয়ে আদালতে রিট পর্যন্ত হয়েছিল। সৈয়দ মনজুরের এক আইনজীবী বন্ধু তাঁর লেখাকে সাক্ষ্য মেনে রিট করলে আদালতে ভাষার বিশৃঙ্খলা রোধে অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের নেতৃত্বে একটি কমিটি করে দেন। এরপর কাকতালভাবে এফএম রেডিও ও টিভি নাটকে ভাষার বিভ্রাট অনেকটা দূর হয়।
তিনি সমাজের রোগ চিহ্নিত করে নিরাময়ের চেষ্টা করতেন। তিনি বিপ্লবী ছিলেন না, ছিলেন প্রগতির অভিযাত্রী।
সৈয়দ মনজুর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন। তিনি মনে করতেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা পাসের চেয়ে জ্ঞান সৃজন ও জ্ঞান বিতরণের ওপরই জোর দেওয়া উচিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা যখন সবকিছু বাদ দিয়ে বিসিএস পরীক্ষার জন্য সমস্ত শক্তি ও মেধা ব্যয় করেন, তখন তা তাঁকে বিচলিত ও ক্ষুব্ধ করত।
শিক্ষার্থীদের এই প্রবণতার বিরুদ্ধে ঠাট্টা করে লিখেছিলেন, ‘একটি বিসিএস বিশ্ববিদ্যালয় চাই।’
গত এক বছর সৈয়দ মনজুরুল ইসলামকে শ্রেণিকক্ষের বাইরে খুব একটা দেখা যেত না। এটা কি তাঁর স্বেচ্ছা নির্বাসন, না অন্য কিছু?
গত ২৭ সেপ্টেম্বর বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে একটি পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে যা বলেছিলেন, তাতে শিক্ষক ও শিক্ষা নিয়ে তাঁর গভীর উৎকণ্ঠাই প্রকাশ পেয়েছিল।
তিনি বলেন,
“আশাবাদ একটা মোমবাতির মতো। একটা মোমবাতি হাতে থাকলেই হয়। একটা মোমবাতি থেকে অনেকগুলো মোমবাতিতে আলো প্রজ্বলন করা যায়। তো যার হাতে আশাবাদের একটা মোমবাতি আছে, তার পক্ষে গোটা দেশকে জাগিয়ে তোলা সম্ভব। তবে তার জন্য অনেক কাজ বাকি আছে। শিক্ষাটায় আমাদের নজর দিতে হবে। যেটা আবু খালেদ পাঠান হয়তো সমস্ত জীবন চেষ্টাকরেছেন। সেই মাপের শিক্ষকও এখন নেই। ভালো শিক্ষক না হলে ভালো শিক্ষিত ছাত্র-ছাত্রী তৈরি করা যায় না। এটা একেবারে আমার পরীক্ষিত একটা চিন্তা।”
তাঁর প্রশ্ন ছিল—আমাদের প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকরা কত বেতন পান? সংস্কার তো ওইখান থেকেই শুরু করতে হবে। মৌলিক বিষয়গুলো তো আপনাকে দেখতে হবে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা দাবি জানান, তাদের দাবিগুলো মিটে যায়। এখনো দেখছি, বেতন বাড়ানো হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা খুব আনন্দ পাচ্ছেন—তাদেরও বেতন বাড়বে। বেতন তো বাড়া উচিত প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকদের! এই বর্তমান বাজারে যদি তাদের এক লক্ষ টাকা করে মাসে দেওয়া হয়, তাদের থাকার জায়গা দেওয়া হয় মানসম্পন্ন, তাহলে বিসিএস পরীক্ষার জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করার চাইতে এই মেধাবীরা এসে প্রাইমারি স্কুলে ঢুকবে। আপনি ভাবুন, কত বড় একটা বিপ্লব হতে পারে শিক্ষার ক্ষেত্রে! কেউ শোনেননি কথা।
যারা শ্রেণি বৈষম্য নিয়ে নিয়ত গলা ফাটান, শ্রেণিহীন সমাজ বিনির্মাণের কথা বলেন, তাঁদের কেউ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আধপেটে শিক্ষকদের দুঃখ-দুর্দশা এভাবে তুলে ধরেননি।
২.
বিশ্বসাহিত্যের গতিপ্রকৃতি নিয়ে বাংলাদেশে হাতে গোনা যে কজন লেখালেখি করতেন, তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম।
বিক্ষিপ্ত প্রবন্ধ ছাড়াও তিনি আশি ও নব্বই দশকে সংবাদ সাময়িকী-তে ধারাবাহিক লিখেছেন অলস দিনের হাওয়া। শিরোনাম রবীন্দ্রনাথ থেকে ধার করলেও তাঁর সেই লেখায় অলসতার ছাপ ছিল না। তিনি বিশ্বসাহিত্যের গতিপ্রকৃতি ব্যাখ্যার পাশাপাশি অনেক বিখ্যাত লেখকের স্মরণীয় কাজ নিয়ে আলোচনা করেছেন।
অনেকটা হালকা মেজাজে এই লেখা সাহিত্যপ্রেমী তো বটেই, সাধারণ পাঠকেরও দৃষ্টি কেড়েছে। অলস দিনের হাওয়া প্রতি পক্ষে একবার বের হতো। অপর পক্ষে বের হতো সৈয়দ শামসুল হকের হৃদ কলমের টানে। সৈয়দ শামসুল হকের লেখাটি শেষ হলে অপরপক্ষে যোগ দেন অর্থনীতিবিদ সেলিম জাহান।
সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম অলস দিনের হাওয়া কলামে আড়াই শ’র মতো কলাম লিখেছিলেন এবং তাঁর সংগ্রহেও ছিল। কিন্তু ২০০৮ সালে বাসা বদলের সময় সেসব লেখা পুরোনো কাগজ ভেবে কেউ ফেলে দেন।
পরবর্তীকালে অনেক খোঁজাখুঁজি করে ৫০টির মতো লেখা নিয়ে বই করেন শুদ্ধস্বর-এর মালিক আহমেদুর রশীদ চৌধুরী টুটুল। কিন্তু বাজারজাত করতে পারেননি। তাঁর আগেই তাঁকে হিংস্র হামলার শিকার হতে হয়। পরে তিনি দেশান্তরি হলে শুদ্ধস্বর-এর প্রকাশনাও বন্ধ হয়ে যায়।
২০১৯ সালে অলস দিনের হাওয়া-র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করে অরিত্র। সংবাদ-এর তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক খোন্দকার মুনীরুজ্জামান এর উদ্যোক্তা ছিলেন। এই প্রকাশনা সংস্থাটিও দীর্ঘ আয়ু পায়নি, করোনা মহামারিতে তাঁর অকাল প্রয়াণের কারণে। ফলে অলস দিনের হাওয়া দ্বিতীয়বার দুর্বিপাকে পড়ে।
সৈয়দ মনজুর অলস দিনের হাওয়ায় শেকসপীয়র থেকে সিলভিয়া প্লাথ, সালমান রুশদি থেকে গুন্টার গ্রাস—বিশ্বসাহিত্যের প্রায় সব সেরা লেখকই স্থান পেয়েছেন। তাঁর সমালোচনার বাইরে থাকেননি নোবেল বিজয়ী ভি. এস. নাইপল, আন্দ্রে মালরো, মিলান কুন্ডেরার মতো দামি লেখকও।
তিনি স্পেনিশ ভাষা না জানলেও ইংরেজি অনুবাদে তুলে এনেছেন লাতিন আমেরিকার শ্রেষ্ঠ লেখক-কবিদের। তাঁর লেখক তালিকায় অনায়াসে জায়গা করে নিয়েছেন গাব্রিয়েল ওকারা, হিমেনেস বোর্হেস, এডওয়ার্ড সাঈদ, রবার্ট ব্লাই, অক্টাভিও পাজ ও গার্সিয়া মার্কেস।
তাঁর গল্প-উপন্যাস পড়লেও লাতিন আমেরিকার লেখকদের ছায়া পাওয়া যায়। তিনি বিশেষভাবে টান অনুভব করতেন নির্বাসিত লেখক-কবিদের প্রতি, যে তালিকায় আছেন আগুস্ত রোয়া বাস্তোস, কাব্রেরা ইনফান্তে।
শেষোক্ত কথাসাহিত্যিক কিউবার বিপ্লবের সমর্থক হয়েও নিগৃহীত হয়েছেন কমিউনিস্ট শাসকদের হাতে; তিনি হাভানাকে তুলনা করেছেন নরকের সঙ্গে। সৈয়দ মনজুর লিখেছেন—
“কাব্রেরা ইনফান্তে কিন্তু ভুলতে পারেননি তাঁর অনুজ কিউবার জনগণকে। কিউবাসী দেখলেন কিন্তু কাস্ত্রোর চোখে রুমাল বেঁধে রাখতে পছন্দ করলেন। কাব্রেরা ইনফান্তে তাই শুরু করলেন তাঁর থ্রি ট্র্যাপড টাইগারস, প্রথমে ভিন্ন নামে; পরিচ্ছদ অনুযায়ী পরে ওই নামে।” (কাব্রেরা ইনফান্তের জগৎ)
অনেক দিন ধরেই যে সাহিত্য নোবেল পুরস্কারের মধ্যে রাজনৈতিক বিবেচনা কাজ করছিল, সেই নিগূঢ় সত্যটি সৈয়দ মনজুর তুলে ধরেছেন একাধিক লেখায়।
তিনি লিখেছেন—
“সেপ্টেম্বর ১১ পরবর্তী বিশ্বে ইসলাম নিয়ে আলোচনার একটা ঝোঁক উঠেছে। পশ্চিমা, বিশেষ করে মার্কিন ও ব্রিটিশ মিডিয়াতে সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে ইসলামকে এক করে দেখার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই পরিস্থিতি সুস্থ চিন্তাভাবনার অনুকূল নয়। এই প্রেক্ষাপটে নাইপলের পুরস্কারপ্রাপ্তি ইসলামের প্রতি সহানুভূতিশীল মহলে একটা অস্বস্তির জন্ম দিতে পারে—যে ইসলামকে একহাত নিল পশ্চিম। নাইপলের বিয়ন্ড বিলিফ-এ যে ইসলাম সম্পর্কে বিদ্বেষ আছে, তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই।”
সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের সাহিত্যকীর্তি নিয়ে ভবিষ্যতে বিস্তারিত লেখার ইচ্ছে আছে। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আজকের লেখাটি শেষ করছি।