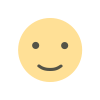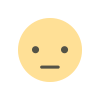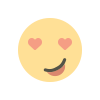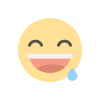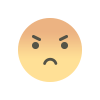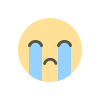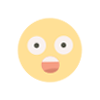অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রনায়ক বঙ্গবন্ধু । আলমগীর শাহরিয়ার
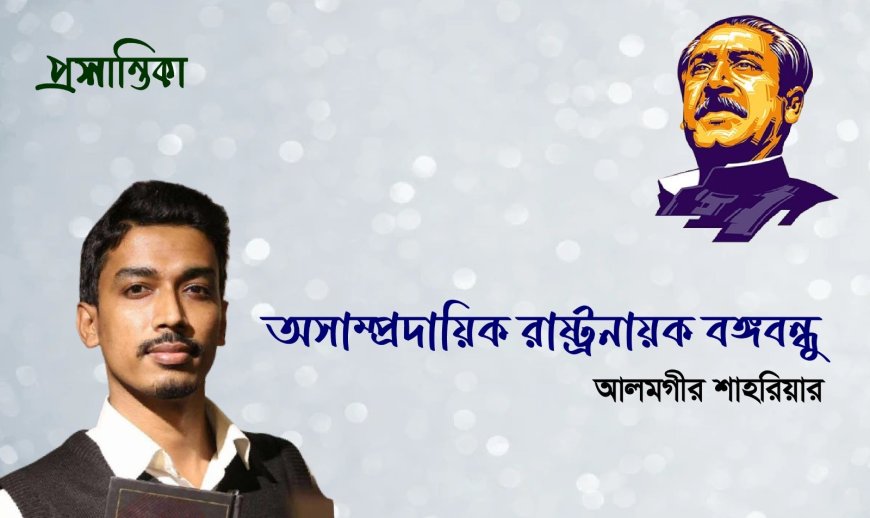
বাংলাদেশ তো বটেই, ভারতীয় উপমহাদেশ এমনকি গোটা বিশ্বে অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির একজন শক্তিমান নেতা ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। আদিম বিশ্বাস, ধর্মান্ধতা, প্রাচীন সংস্কারের বেড়াজাল, মধ্যযুগের ধর্মযুদ্ধকাল পেরিয়ে রেনেসাঁ-আলোকিত এবং শিল্পবিপ্লবোত্তর পৃথিবী প্রধানত দুই বলয়ে বিভক্ত ছিল—পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব বনাম সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব। এই দুই বলয়ের মধ্যে প্রায় অদৃশ্য আরেকটি পক্ষ ছিল ধর্মবিপ্লবে বিশ্বাসী শক্তি, যাদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছে সুবিধামতো উভয় পক্ষই।
এরকম বহুধা বিভক্ত সময়ে ভারতবর্ষ স্বাধীন হলো এবং একই সঙ্গে ধর্মজিগির তুলে বিভক্ত হলো। পাকিস্তান ছিল একটি ধর্মকল্পিত রাষ্ট্র। সেই পাকিস্তান আন্দোলনে তরুণ শেখ মুজিব নিজেও অংশ নিয়েছিলেন। কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টির পর অচিরেই তাঁরও ভুল ভাঙলো। ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তাঁর অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির পথচলা ক্রমশ স্পষ্ট হতে থাকে।
বাংলাদেশে শেখ মুজিবের ইতিহাস মূলত চব্বিশ বছর সেনা-সমর্থিত ধর্মরাষ্ট্র পাকিস্তানের বঞ্চনা, শোষণ আর নিপীড়নের বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকার ইতিহাস। একাত্তরের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বিশ্বের বুকে একটি নতুন রাষ্ট্রেরই শুধু অভ্যুদয় হলো না, একই সঙ্গে একজন শক্তিমান অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রনায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানেরও আবির্ভাব হলো।
বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিক্সের সাউথ এশিয়া সেন্টার আয়োজিত এক আলোচনা সভায় নোবেলজয়ী বাঙালি অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন মুক্তিযুদ্ধ-উত্তর প্রণীত বাংলাদেশের সংবিধানের দুটি মূলমন্ত্র—সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা—হাইলাইট করে বলেন:
“সমাজে সমতা প্রতিষ্ঠা এবং ধর্মকে রাজনীতির বাইরে রাখার ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যে মতাদর্শ, তা এখনও সারা পৃথিবীর জন্য প্রাসঙ্গিক। বঙ্গবন্ধুর সেকুলারিজম ধারণার মানে মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতা থাকবে না, এমন নয়। সেটা ছিল ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার হবে না। সংবিধান প্রণয়নের সময় বলা হয়েছিল, এটা এমন নয় আমরা ধর্মপালন বন্ধ করব। মুসলমান, হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ সবাই তার ধর্ম পালন করবে। কেবল ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার বন্ধ থাকবে।”
ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রসঙ্গে অমর্ত্য সেন ষোড়শ শতকের সম্রাট আকবরের মতাদর্শের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর দর্শনের মিলও খুঁজে পান। তাঁর মতে, বঙ্গবন্ধু ও আকবরের মতাদর্শ আজও বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, শুধু ভারতবর্ষ নয়, বিশ্বের অন্যান্য দেশেও প্রাসঙ্গিক।
পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্ট হয়েছিল ধর্মের জিগিরে। পরিহাসের বিষয় হলো, এই ধর্মান্দোলনের নেতৃত্বে থাকা মুহম্মদ আলী জিন্নাহ ব্যক্তিজীবনে ধর্মকর্মের ধার ধারতেন না। তিনি ছিলেন আপাদমস্তক পশ্চিমা জীবনধারায় অভ্যস্ত। জিন্নাহ ছাড়াও পাকিস্তান আন্দোলনের অন্যতম শীর্ষ নেতা শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক কিংবা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী—কেউই প্র্যাকটিসিং মুসলিম ছিলেন না।
১৯৪৭ সালে ধর্মজিগিরে দেশভাগ ও পাকিস্তান সৃষ্টিই উপমহাদেশের মানুষকে, সমাজকে, সংস্কৃতিকে চিরকালের জন্য বিভক্ত করে দিয়েছিল। হয়তো নানা সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে সেটাই ইতিহাসের পথে অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। কিন্তু একাত্তরে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ও বঙ্গবন্ধুর আধুনিক রাষ্ট্রদর্শন—যার ভিত্তি ধর্মনিরপেক্ষতা—উপমহাদেশের রাজনীতির গাঢ় অন্ধকারে আলো ও আশার সঞ্চার করে।
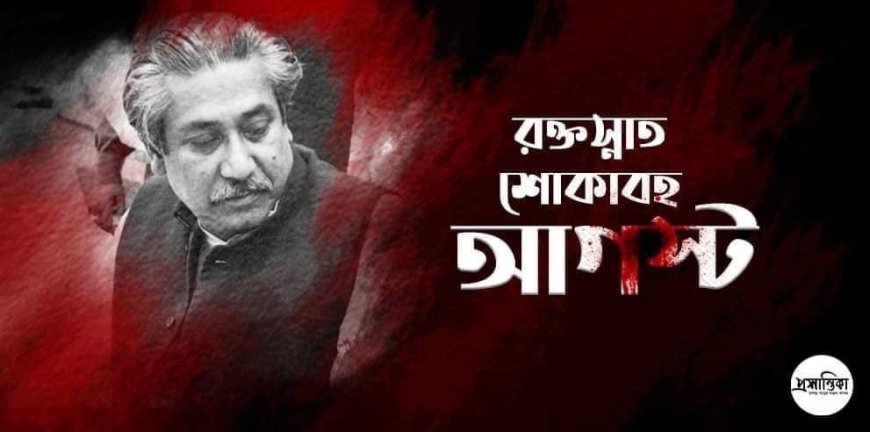
আওয়ামী লীগের রাজনীতির অন্যতম মূলমন্ত্র ধর্মনিরপেক্ষতা নানা সময়েই অপপ্রচারের শিকার হয়েছে। মৌলবাদী শক্তি ধর্মনিরপেক্ষতাকে ধর্মহীনতা হিসেবে আখ্যায়িত করার প্রাণপণ চেষ্টা করেছে, এখনও করছে। প্রথাবিরোধী লেখক হুমায়ুন আজাদ বলেছিলেন:
“ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ হচ্ছে সমাজে ধর্ম থাকবে। যার ইচ্ছা পালন করবে, যার ইচ্ছা পালন করবে না। রাষ্ট্র কোনো পক্ষ নেবে না এবং যারা ধর্ম পালন করে না তাদের পীড়ন করবে না।”
১৯৭২ সালের সংবিধান নিয়ে সংসদে বক্তৃতা করার সময় বঙ্গবন্ধুও একই কথা বলেছিলেন:
“জনাব স্পিকার সাহেব, ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের ধর্মকর্ম করার অধিকার থাকবে। আমরা আইন করে ধর্মকে বন্ধ করতে চাই না এবং করবও না। মুসলমানরা তাদের ধর্ম পালন করবে, তাদের বাধা দেওয়ার ক্ষমতা এই রাষ্ট্রের কারও নাই। হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সবাই তাদের ধর্ম পালন করবে, কাউকে বাধা দেওয়া যাবে না। আমাদের আপত্তি শুধু এই যে, ধর্মকে কেউ রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে না। ধর্ম নিয়ে ব্যবসা করতে পারবে না।”
নতুন শতাব্দীর শুরুতে লেখক স্মৃতিচারণ করেছেন—সিলেটে শহিদ মিনারের কাছে এক সভায় শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক হাবিবুর রহমানের বক্তব্য শুনেছিলেন: “রাষ্ট্রের কোনো ধর্ম নেই। ব্যক্তির ধর্ম থাকতে পারে, বিশ্বাস থাকতে পারে। রাষ্ট্র সকল মানুষের।” এই ভাবনাও বঙ্গবন্ধুর অসাম্প্রদায়িক দর্শনের সঙ্গে মিলে যায়।
বঙ্গবন্ধু চল্লিশের দশকে ব্রিটিশ শাসনের কূটকৌশলে বেড়ে ওঠা ধর্মরাজনীতির মিছিলের সময়েই রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন। সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে মুসলিম লীগ সংগঠিত করেছিলেন। দাঙ্গা ও তার ভয়াবহতা তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন।
তবু তাঁর রাজনৈতিক মনস্তত্ত্বে প্রভাব ফেলেছিল অন্যরকম প্রেরণা—স্বদেশি আন্দোলন ও নেতাজি সুভাষ বসুর প্রতি মুগ্ধতা। নিজের অসমাপ্ত আত্মজীবনী গ্রন্থে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন:
“আমিও সুভাষ বাবুর ভক্ত হতে শুরু করলাম। সভায় যোগ দিতে মাঝে মাঝে গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর যাওয়া-আসা করতাম। আর স্বদেশি আন্দোলনের লোকদের সঙ্গেই মেলামেশা করতাম।”
বঙ্গবন্ধু যখন আওয়ামী লীগ গড়ে তুললেন, দলটি মুসলিম লীগের সংকীর্ণ দর্শন থেকে বেরিয়ে এলো। ১৯৫৫ সালের তৃতীয় সম্মেলনে দলটির নাম থেকে ‘মুসলিম’ শব্দ বাদ দিয়ে সর্বজনীন করা হয়—‘পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ’। এটি ছিল অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির পথে একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক, যার ধারাবাহিকতায় একাত্তরে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয়।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান, অসাম্প্রদায়িক মানবতাবাদ ও গণতান্ত্রিক চেতনা বঙ্গবন্ধুর রাজনীতিতে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। জাতীয় সংগীত হিসেবে আমার সোনার বাংলা বেছে নেওয়ার মধ্যেই তিনি তা প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর নেতা সোহরাওয়ার্দীও গণতন্ত্র ও অসাম্প্রদায়িকতার প্রতীক ছিলেন। সত্তরের নির্বাচনের ইশতেহার এবং ১৯৭২ সালের সংবিধানেও সেই অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত হয়েছিল।
১৯৭৪ সালে আওয়ামী লীগের কাউন্সিলে বঙ্গবন্ধু স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন:
“রাজনীতিতে যারা সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করে, তারা হীন, নীচ, তাদের অন্তর ছোট। যে মানুষকে ভালোবাসে, সে কোনোদিন সাম্প্রদায়িক হতে পারে না। তোমরা জীবনভর সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছ, জীবন থাকতে কেউ যেন বাংলার মাটিতে সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন না করতে পারে।”
আগস্ট ২০২৫—বঙ্গবন্ধু হত্যার পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হচ্ছে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সপরিবারে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ড ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধবিরোধী শক্তির প্রতিশোধ। পঞ্চাশ বছর পর, ২০২৪ সালের আগস্টে তাঁর ৩২ নম্বর বাড়ি—যেটি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের অমূল্য স্মৃতিসংবলিত জাদুঘর—আগুন দিয়ে ধ্বংসের চেষ্টা করা হয়েছিল।
কিন্তু ইতিহাস জানে—যার নাম এবং দেশের নাম অভিন্ন হয়ে যায়, তাঁকে হত্যা করে মুছে ফেলা যায় না।
আগস্ট ফিরে এলেই
বত্রিশ নম্বরের লেক হয়ে ওঠে বেদনার অতলান্ত নদী
যে নদী কাঁদে বঙ্গোপসাগর অবধি।
ঢেউয়ে ঢেউয়ে গর্জে ওঠে সমুদ্রের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ
মুক্তিকামী মানুষের ভিড় বাড়ে—আসমুদ্রহিমাচল।
ওই দ্যাখো—রেসকোর্স জনসমুদ্রে স্বাধীনতার ডাক দেয়,
দাসত্বের শৃঙ্খল ভাঙা
শেখ মুজিবের আকাশছোঁয়া তর্জনী—
যাকে মুছে দিতে পারেনি
আগস্ট থেকে আগস্টের নিকষ কালো রজনী।
আলমগীর শাহরিয়ার : বিলেত প্রবাসী বাঙালি কবি, প্রাবন্ধিক ও গবেষক। পড়াশোনা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাজবিজ্ঞান বিভাগে। ঢাকায় একটি জাতীয় দৈনিকে সাংবাদিকতা দিয়ে পেশাজীবন শুরু। আন্তর্জাতিক একটি প্রতিষ্ঠানে গবেষণা-সহযোগী এবং সর্বশেষ, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে কাজ করেছেন দীর্ঘদিন। অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের একান্ত সচিব হিসেবেও কর্মরত ছিলেন। এডুকেশন নিয়ে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করেন ইংল্যান্ডের বার্মিংহাম সিটি ইউনিভার্সিটি থেকে। বর্তমানে বার্মিংহাম শহরে বসবাস করছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে প্রকাশিত তার উল্লেখযোগ্য গবেষণাগ্রন্থ “রবীন্দ্রনাথ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িকতা”। তাঁর প্রকাশিত একাধিক কাব্যগ্রন্থও রয়েছে।